১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তিনটি ঘটনা ঘটেছিল। বসেছিল প্রাদেশিক পরিষদের সভা, ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা করেছিলেন ১৪৪ ধারা, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভাঙা না-ভাঙার ব্যাপারে বৈঠকে বসেছিল।

হিন্দি না উর্দু—জাতীয় ভাষা কোনটা হবে, এ নিয়ে বিতর্ক চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। হিন্দু নেতারা চাইছিলেন হিন্দি হোক ভারতের জাতীয় ভাষা, আর মুসলমান নেতারা চাইছিলেন জাতীয় ভাষা হোক উর্দু। ভারত আর পাকিস্তানে দেশটা বাঁটোয়ারা হয়ে যাওয়ার অনেক আগের কথা সেটা। বাংলা প্রসঙ্গটি তখন সেভাবে আসেনি...

ভাষা নিয়ে কিছু বলতে গেলে সে সময়ের সমাজ নিয়েও কথা বলতে হয়। কীভাবে বাংলা ভাষা জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলের ভাষা হয়ে উঠল, কীভাবে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে দেশের জনগণ বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রস্তুত হলো, তার পটভূমি জানা দরকার।

ব্রিটিশ আমলের শুরুর দিক পর্যন্ত বহিরাগত অভিজাত মুসলমানেরা নিজেদের মনে করত পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর অংশ। দেশীয় মুসলমানেরা এই পরিচয়ের ক্ষেত্রে ছিল উদাসীন। কারণ তাতে তাদের কিছুই আসত-যেত না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে দেশীয় মুসলমানেরাও মনে করতে শুরু করল, যেহেতু এককালে মুসলমানেরাই ছিল...

বাঙালি মুসলমানের মনে একটা অদ্ভুত ধারণা ভিত্তি পেয়েছে। তাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ব্রিটিশ যুগে এসেই মুসলমানরা বঞ্চিত হয়েছে। তুর্কি-মোগলদের শাসনামলে বাঙালি মুসলমানরা ধনে-মানে-শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে এগিয়ে ছিল। ব্রিটিশরা এসে তাদের সেই অবস্থা থেকে টেনে নামিয়েছে। আর তারই সুযোগ নিয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে বিদেশে’ বইয়ের হরফুন মৌলা বা সকল কাজের কাজী আবদুর রহমানের বলা একটি বাক্য—‘ইনহাস্ত ওয়াতানাম’—‘এই আমার জন্মভূমি’। সে কথা বলার সময় আফগানি আবদুর রহমানের চোখেমুখে যে অম্লান দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছিল, সে কথা দিব্যি অনুভব করে নেওয়া যায়...
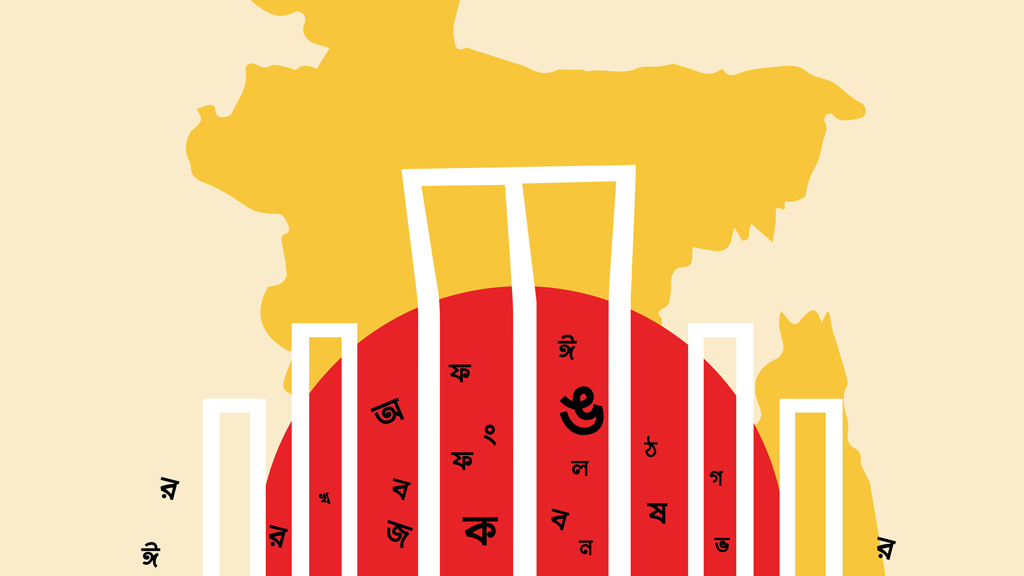
স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে একটা নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরেও একুশে ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন বিষয়টি আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ, আজকেও আমাদের কাছে এর আবেদন বহমান, আজকেও আমাদের ডাকে, আমাদের মনে এক অনুভূতি সৃষ্টি করে। কেন করে? সে কি শুধু এ কারণেই করে যে, বাংলা ভাষা শিক্ষার সর্বস্তরে প্রযুক্ত হয়নি? স
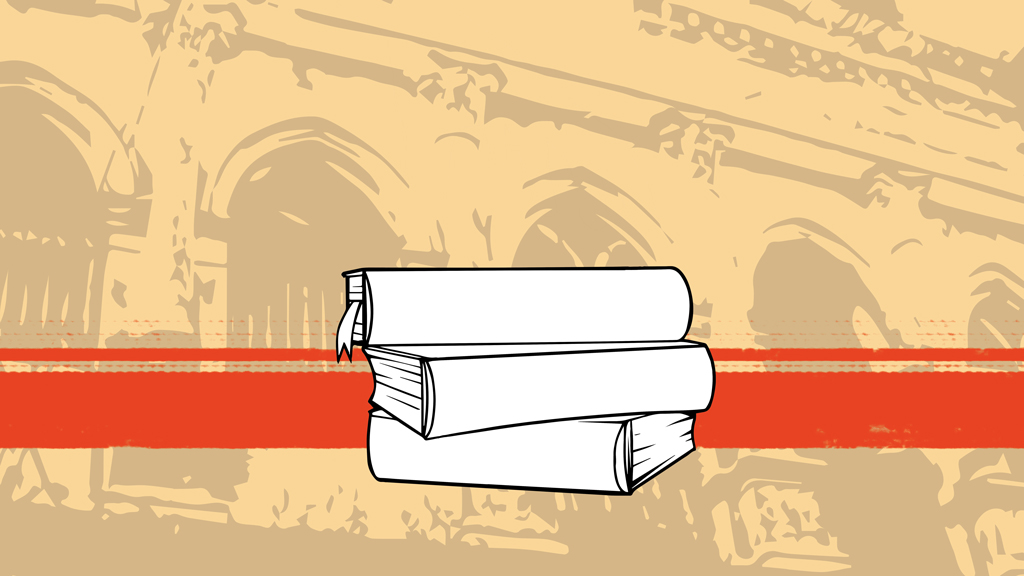
ইতিহাস চর্চার ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরোনো হলেও বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত খুব বেশি দিনের নয়। ঔপনিবেশিক শাসনামলেই বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চার ধারা শুরু হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর গবেষকদের হাতে যখন ভারতবিদ্যার জ্ঞান বিস্ফোরিত হচ্ছিল, তখন থেকেই ইতিহাস চর্চার ধারা শু

বাংলাদেশ বিপ্লবের তিনটি পর্যায় হলো—ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন তথা ছয় দফা ও এগারো দফার গণ-অভ্যুত্থান এবং মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ। এই বিপ্লবকে একটি জৈবিক সত্তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮–১৯৫২) ছিল জৈবিক ভ্রূণের সঙ্গে তুলনীয় এক প্রাথমিক সত্তা অথবা অস্তিত্ব।

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া নিয়ে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের দুই দলে মধ্যে হট্টগোল হয়েছে।

নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে। বুধবার সকালে রাজধানীর আফতাবনগরে ‘প্রভাত ফেরি’ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্মিত ‘শহীদ মিনার’-এ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়

আজীমপুর কবরস্থানের দক্ষিণ দরজা দিয়ে ঢুকে সামান্য হাটতে হবে ৷ তারপর বামপাশে তাকালেই চোখে পড়বে সাদা-কালো মার্বেল পাথরে বাঁধাই করা পাশাপাশি তিনটি সমাধি ৷ মায়ের ভাষায় কথা বলতে আর স্বাধীন আশায় পথ চলার দৃপ্ত প্রত্যয় জারি রাখতে যারা

পাহাড়ি অঞ্চলের হাজং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসেছে। এই ভাষা টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অন্তর হাজং। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে নিজের গোত্রের বিভিন্ন বয়সীদের হাজং ভাষা শেখাচ্ছেন তিনি।
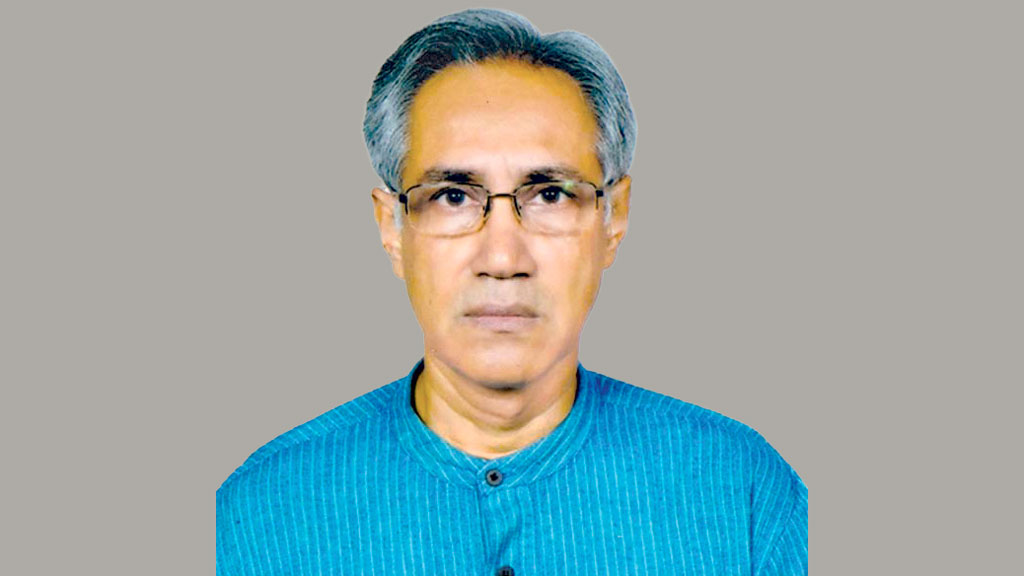
ফেব্রুয়ারি এলেই বাংলা ভাষা নিয়ে হইচই আর সাদাকালো পোশাক নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়ে যায়। তারপর আবার পরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নীরবতা। মাঝখানে পয়লা বৈশাখে আবার বাঙালিত্ব জেগে ওঠে। লাল-সাদা পোশাক নিয়ে পান্তা-ইলিশ। এতে দোষের কিছু নেই; বরং সংস্কারমুক্ত দুটো বিষয় বাঙালিদের অল্প সময়ের জন্য হলেও এক ও ধর্মনিরপেক্ষ

আজ অমর একুশে। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এই দিন রক্ত ঝরেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পঞ্চম বছরে এসেই সন্দেহ, অবিশ্বাস আর শোষণ-বঞ্চনার বিষয়গুলো স্পষ্ট হতে থাকে।

ভাষা আন্দোলনের সাত দশক পেরিয়ে গেলেও সাতক্ষীরার ৭৩ শতাংশেরও বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা হয়নি কোনো শহীদ মিনার। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি পালনে অস্থায়ীভাবে শহীদ মিনার নির্মাণ করে কাজ চালাতে দেখা যায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে। অন্যদিকে বরগুনার আমতলী উপজেলায় ৮৭ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শহীদ ম

যখন ১৪৪ ধারা ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা থেকে ১০ জনি মিছিলগুলো বেরোচ্ছিল, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন কী করছিলেন? তিনি যদি তখন বলিষ্ঠ কোনো অবস্থান নিতে পারতেন, তাহলে কি সেদিন গুলিবর্ষণ হতো না? দিনটি হতে পারত অন্য রকম?